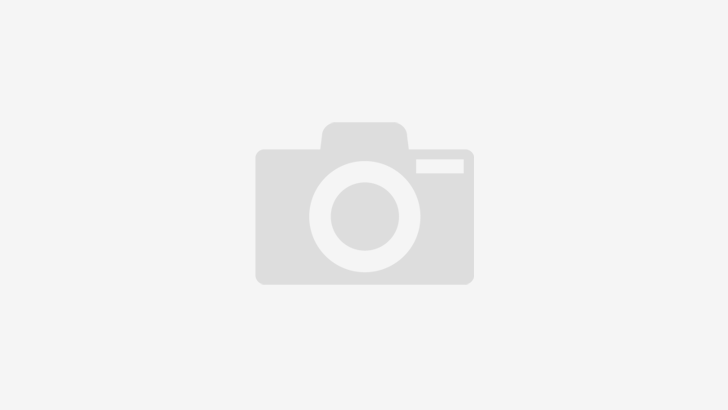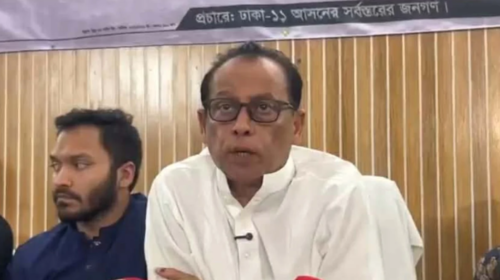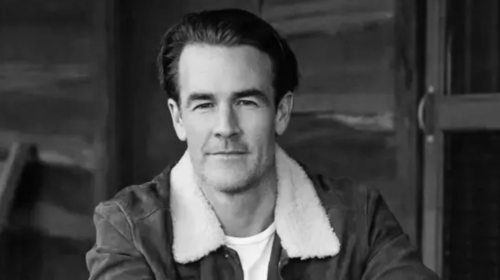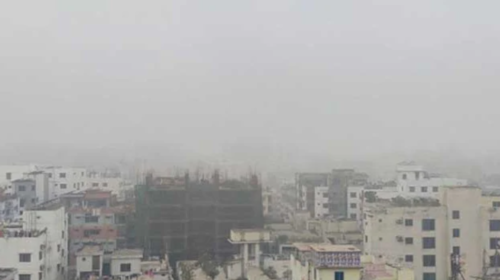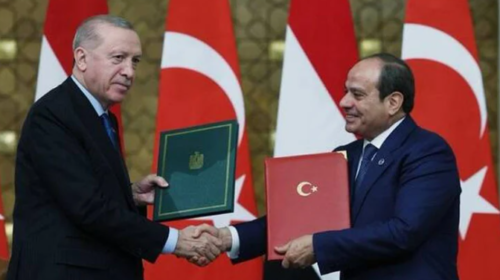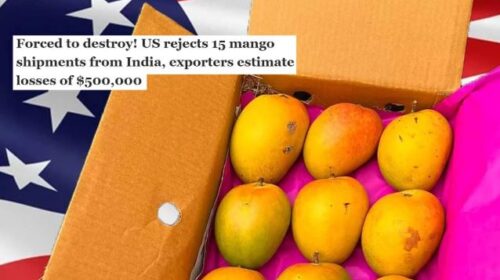ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ২০২০ সালে তার লেখা ‘দ্য ইন্ডিয়া ওয়ে: স্ট্র্যাটেজিস ফর অ্যান আনসার্টেইন ওয়ার্ল্ড’-এ লিখেছেন, ‘এটা এমন এক সময়, যখন আমাদের দরকার আমেরিকার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক, চীনকে সামলানো, ইউরোপকে আকৃষ্ট করা, রাশিয়াকে আশ্বস্ত করা, জাপানকে খেলায় আনা, প্রতিবেশীদের যুক্ত করা এবং সমর্থনের ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত করা।’এমন পরিস্থিতিতে আগামীকাল রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বেইজিং সফর এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠক অনেকের চোখে কৌশলগত পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে।কিন্তু সবকিছুর পরেও দিল্লির পররাষ্ট্রনীতি একটি অস্বস্তিকর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।ভারত একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইন্দো-প্যাসিফিক কোয়াডের স্তম্ভ। আবার সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সদস্য। চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন এই ব্লক প্রায়ই মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করে। ভারত রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনছে, আবার মার্কিন বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিকে আকর্ষণে কাজ করছে এবং আগামী সপ্তাহে তিয়ানজিনে এসসিও টেবিলে বসারও প্রস্তুতি নিচ্ছে।
২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষের পর জমে থাকা উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত করার লক্ষ্যে মোদীর চীন সফরকে অনেকেই কৌশলগত বিরতি হিসেবে দেখছেন।
সম্পর্কের পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরে দিল্লিতে চীনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের ওপর ওয়াশিংটনের উচ্চ শুল্ক আরোপের সমালোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্র ‘দাদাগিরি’ করছে বলেও অভিহিত করেন তিনি। গত সপ্তাহে চীনের রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং অংশীদার’ বলে উল্লেখ করেন।তবে সমালোচকদের প্রশ্ন- কেন এখনই নয়াদিল্লি বেইজিংয়ের সঙ্গে কৌশলগত সংলাপে বসছে? বিশ্লেষক হ্যাপিমন জ্যাকবের ভাষায়, ‘বিকল্প কী?’ পরবর্তী কয়েক দশক ধরে চীনকে সামলানোই ভারতের মূল কৌশলগত ব্যস্ততা।
হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার একটি পৃথক প্রবন্ধে, জ্যাকব দিল্লি এবং বেইজিংয়ের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনাকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরেন যাকে তিনি ভারত, চীন এবং রাশিয়ার ত্রিপক্ষীয় আন্তঃসম্পর্ক বলে উল্লেখ করেন।
তিনি উল্লেখ করেন যে, এই ত্রিমুখী আলোচনা মার্কিন নীতির প্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর পুনর্বিন্যাসকে প্রতিফলিত করে এবং দিল্লি এবং বেইজিংকে ওয়াশিংটনকে ইঙ্গিত দেওয়ার সুযোগ দেয় যে বিকল্প ব্লক সম্ভব।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউশনের সুমিত গাঙ্গুলি যেমন উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ‘কাঠামোগতভাবে অমীমাংসিত’ রয়ে গেছে, অন্যদিকে রাশিয়া বেইজিংয়ের ‘জুনিয়র পার্টনার’ হয়ে উঠেছে। এই পটভূমিতে, ভারতের কৌশলগত সুযোগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি, ভারতের বর্তমান কৌশল হলো সময় কাটানোর জন্য চীনের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্কের আভাস বজায় রাখার চেষ্টা করা।
রাশিয়ার তেল কেনার কথা বলতে গেলে উল্লেখ করা যায় যে, ভারত মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করার খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। মস্কো থেকে ছাড় পাওয়া অপরিশোধিত তেল জ্বালানি নিরাপত্তার মূল বিষয়। জয়শঙ্করের সাম্প্রতিক মস্কো সফর ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এবং চীনের ওপর রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার পরেও দিল্লি এখনো সম্পর্ক উষ্ণ রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।
পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধের অবসানে মধ্যস্থতার জন্য ট্রাম্পের বারবার দাবি দিল্লিকে বিরক্ত করেছে। অন্যদিকে ভারতের কৃষি বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকারের দাবির কারণে একটি বহুল আলোচিত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বৃহত্তর স্বার্থ ঝুঁকির মুখে থাকাকালীন গুরুতর ফাটলও সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। আমরা পরবর্তী কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি।
তিনি ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৯৮ সালে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার পর ওয়াশিংটনের কঠোর নিষেধাজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, দিল্লিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল এবং বছরের পর বছর ধরে সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল। কিন্তু এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ একটি ঐতিহাসিক বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছিল, যা কৌশলগত যুক্তির দাবিতে উভয় পক্ষের অবিশ্বাস কাটিয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছে।
বিশ্লেষকরা এখন যেমন যুক্তি দিচ্ছেন, সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হবে কি না তা নয় বরং তাদের কী রূপ নেওয়া উচিত সেটাই এখন গভীর প্রশ্ন।
তিনি বলেন, যেহেতু আমেরিকা আপেক্ষিক পতনের পরেও এশিয়ার শীর্ষ দুই দেশকে পরাজিত করবে, তাই চীনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভারতের ওয়াশিংটনের সঙ্গে ‘সুবিধাপ্রাপ্ত অংশীদারত্ব’ দৃঢ় করা উচিত। তিনি সতর্ক করে বলেন, দিল্লি এমনটা না করলে তা ‘প্রতিকূল পরাশক্তির’ মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।
কিন্তু বেইজিং এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নিরুপমা রাও বলেন, ভারত ক্রিসালিসের মতো এক টাইটান- এত বিশাল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে কোনো একক বৃহৎ শক্তির সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে না। এর ঐতিহ্য এবং স্বার্থ এমন একটি বিশ্বে নমনীয়তা দাবি করে, যা দুটি শিবিরে বিভক্ত নয় বরং আরও জটিল উপায়ে ভেঙে পড়ছে। তিনি যুক্তি দেন যে কৌশলগত অস্পষ্টতা দুর্বলতা নয় বরং স্বায়ত্তশাসন।
এই দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, একটি জিনিস স্পষ্ট তা হচ্ছে, চীন নেতৃত্বাধীন, রাশিয়া-সমর্থিত, নন-আমেরিকান বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ে দিল্লি গভীরভাবে অস্বস্তিতে রয়েছে।
সুমিত গাঙ্গুলি বলেন, সত্যি বলতে, ভারতের পছন্দ সীমিত। চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো সম্ভাবনা নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা টিকে থাকবে।”
তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে, তবে কেবল কিছু সময়ের জন্য। ওয়াশিংটনের কথা বলতে গেলে, যদিও ট্রাম্প আরও তিন বছর বা তারও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও মার্কিন-ভারত সম্পর্ক টিকে থাকবে। কিন্তু ট্রাম্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয় দেশেরই সম্পর্ক ভেঙে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।